ছোটবেলার শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সাজানো এই লেখাটি[১] শুরু করব প্রয়াত মা-বাবা সরলিকা ও ব্রজেন্দ্রনাথ ত্রিপুরার কথা দিয়ে, যাঁরা ছিলেন আমার ও আমার ভাইদের প্রথম শিক্ষক। অন্য দশজন বাবা-মায়ের মতই তাঁদেরও স্বপ্ন ছিল সন্তানেরা লেখাপড়া শিখে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষের মত মানুষ হবে। তাঁদের সেই স্বপ্ন আমরা, তাঁদের সন্তানেরা, কতটুকু বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছি, তা আমরা নিজেরা বিচার করতে পারি না। তবে আমরা এটুকু বলতে পারি, মনের গভীরে আমরা লালন করে চলছি তাঁদের শেখানো কিছু নীতি ও আদর্শ, কিছু পথের নিশানা। বাবা-মা দু’জনেই আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে, এবং শিক্ষকদেরকে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে বসাতে।
বাবা ছিলেন এমন এক প্রজন্মের মানুষ, যাঁদের ছোটবেলায় খাগড়াছড়ি ছিল স্রেফ প্রত্যন্ত এলাকার একটি কৃষিনির্ভর জনপদ, যা প্রশাসনিক ভাবে ছিল রামগড় মহকুমা ও মহালছড়ি থানার আওতাধীন। তখন খাগড়াছড়িতে, বিশেষ করে ত্রিপুরাদের মধ্যে, শিক্ষার প্রতি তেমন অনুরাগ ছিল না। তবে আমাদের পিতামহ জাংগারায় কার্বারি কিভাবে যেন শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, অন্তত ছেলেদের বেলায়। সন্তানদের নিয়ে জাংগারায়ের স্বপ্ন কি ছিল আমরা জানি না, তবে তাঁর ছেলে ব্রজেন্দ্র নাথ কর্মজীবন শুরু করেন একজন শিক্ষক হিসেবে, বর্তমানে যেটি খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সেখানে। পরে ‘ওয়েলফেয়ার অফিসার’ পদে চাকরি পাওয়ার সুবাদে খুব বেশিদিন তিনি শিক্ষকতা করেননি, তবে তিনি চেষ্টা করেছিলেন নিজের পরিসরে কাজ করেই সমাজে শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখতে।
মায়ের কথা বলতে গেলে শুরুতেই উল্লেখ করতে হয়, তিনি ছিলেন এমন এক সময়ের মানুষ যখন মেয়েদের লেখাপড়াকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হত না। সে কারণে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডীও পার হননি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। নতুবা সেকালের একজন হেডম্যানের কন্যা হিসেবে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তত আর্থিক কোনো বাধা নিশ্চয় তাঁর ছিল না। যাহোক, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বেশিদূর আগাতে না পারলেও মা ছিলেন স্ব-শিক্ষিত, এবং শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। এজন্যই কিনা জানি না, মার একটি নাম ছিল ‘লেখা’। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা ভাষায় ‘লেখা’ শব্দটি দিয়ে একাধারে ‘শিক্ষা’, ‘বিদ্যা’, ‘জ্ঞান’ সবই বোঝায়। সেই লেখার পথে চলতে গিয়ে আমার ও আমার ভাইদের কাছে প্রেরণার অফুরান উৎস ছিলেন আমাদের মা, যিনি ছিলেন আমাদের প্রথম ও প্রধানতম শিক্ষক।
খাগড়াপুরে ‘লেখা’র পথে যাত্রা শুরু
খাগড়াপুর এলাকাটি আমাদের অনেকের কাছে কালক্রমে ‘বাংলাদেশে ত্রিপুরাদের রাজধানী’ নামে পরিচিত হয়ে উঠলেও আগে এখানে সে অর্থে শিক্ষার আলো ছিল না। একসময় এখানে কোনো প্রাইমারি স্কুলও ছিল না। মনে পড়ে, আমার বয়স যখন পাঁচের কোঠায় (১৯৬৭ সালের দিকে), গ্রামের সকলে মিলে মহা উৎসাহে একটি স্কুল ঘর বানিয়েছিল, কেউ নিয়ে এসেছিল খুঁটি, কেউবা ছন, কেউ দিয়েছিল শ্রম। স্কুলটা গড়ার পেছনে বাবা ও মায়ের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। শুধু জমি দান বা বুদ্ধি পরামর্শেই তাঁদের ভূমিকা সীমিত ছিল না, স্কুলে কেমন পড়াশুনা হচ্ছে সে বিষয়েও তাঁরা খোঁজখবর রাখতেন। এর একটা কারণ হয়তবা এই ছিল যে, সে স্কুলে তাঁরা তাঁদের ছেলেদেরও দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ স্থানীয় উদ্যোগে গড়া সেই স্কুলে আমার শিক্ষাজীবনের প্রথম দু’টি বছর পার করেছিলাম আমি (আমার ভাইদের মধ্যে সনজীব ও রাজীবও এই স্কুলে পড়েছিল, যেখানে তারা সম্পন্ন করেছিল পুরো প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্ব)। স্কুলটির নাম দেওয়া হয় ‘খাগড়াপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়’। যতদূর মনে পড়ে, ‘খাগড়াপুর’ নামটির উৎপত্তি হয়েছিল স্কুলের নামকরণের সুবাদেই। প্রথা অনুসারে স্কুলটার নাম হতে পারত ‘জাংগারায় কার্বারি পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়’, যেমনটা শুরুতে ভাবা হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ‘খাগড়াছড়ি’র সাথে মিল রেখে তখনকার সমাজপ্রধানদের চিন্তায় একটি আধুনিক গ্রামের পরিচয়বাহী নাম হিসেবে ‘খাগড়াপুর’ নামটি বেছে নেওয়া হয়েছিল।
খাগড়াপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরুতে শিক্ষক ছিলেন দু’জন, প্রয়াত বীর কিশোর ত্রিপুরা এবং প্রয়াত সাধন কুমার ত্রিপুরা, যাঁরা ছিলেন যথাক্রমে আমার বাবার ছোটভাই ও তাঁর বড় ভাইয়ের ছেলে। উভয়ের স্মৃতির প্রতি নিবেদন করছি শ্রদ্ধাঞ্জলি। বাড়িতে আমাকে এবং আমাদের ভাইদের পড়াতেন শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ ত্রিপুরা, যাঁকে আমরা ‘দাদা মাস্তর’ (মাস্টার দাদা) বলে ডাকতাম, যিনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় চাকুরির মেয়াদ শেষ করে বর্তমানে খাগড়াপুরে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন। তাঁকেও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। পরবর্তী জীবনের অন্য শিক্ষকদের কথায় একটু পরে আসছি, তার আগে একটু বলে নেই আমার প্রথম জীবনের সহপাঠীদের কথা, এবং একটু আভাস দেই কোন পরিবেশে তখন আমরা স্কুলে পড়তে শুরু করি।
 খাগড়াপুরে আমার সহপাঠীরা প্রায় সবাই ছিল আমার চেয়ে বয়সে বড়, বিশেষ করে মেয়েরা, যাঁদের দু’একজনকে আমি সম্বোধন করতাম ‘আবৈ’ (দিদি) বা ‘আনৈ’ (পিসী) হিসেবে। সে সময় অভিভাবকদের অনেকে খোলাখুলি বলতেন, মেয়েদের স্কুলে পড়ানোর দরকার নেই। সে অবস্থায় মাকে দেখতাম আত্মীয়-পড়শিদের উৎসাহ দিতে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে শিশুদের স্কুলে পাঠাতে। আমার প্রথম জীবনের সহপাঠীদের মধ্যে দু’একজন আবার অকালে ইহলোক ছেড়ে গেছে। তাদের একজন হল ‘নবামহন’, যার সাথে একদিন গাছে চড়ে বড়ই খেতে খেতে ‘কিচিং’ (আনুষ্ঠানিকভাবে ‘একাত্ম’ হিসেবে বিবেচিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু) সম্পর্ক পাতিয়েছিলাম। অন্য সহপাঠীদের মধ্যে দু’একজনের সাথে কদাচিৎ দেখা হয় এখনো, তবে সবার কথা সেভাবে মনেও নেই আর। আসলে ক্লাস থ্রিতে আমি অন্য স্কুলে চলে যাই, আর আমার খাগড়াপুরের সহপাঠীদের অনেকেই পেছনে থেকে যায়, এমনকি মাঝপথে পড়াশুনাই ছেড়ে দেয়।
খাগড়াপুরে আমার সহপাঠীরা প্রায় সবাই ছিল আমার চেয়ে বয়সে বড়, বিশেষ করে মেয়েরা, যাঁদের দু’একজনকে আমি সম্বোধন করতাম ‘আবৈ’ (দিদি) বা ‘আনৈ’ (পিসী) হিসেবে। সে সময় অভিভাবকদের অনেকে খোলাখুলি বলতেন, মেয়েদের স্কুলে পড়ানোর দরকার নেই। সে অবস্থায় মাকে দেখতাম আত্মীয়-পড়শিদের উৎসাহ দিতে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে শিশুদের স্কুলে পাঠাতে। আমার প্রথম জীবনের সহপাঠীদের মধ্যে দু’একজন আবার অকালে ইহলোক ছেড়ে গেছে। তাদের একজন হল ‘নবামহন’, যার সাথে একদিন গাছে চড়ে বড়ই খেতে খেতে ‘কিচিং’ (আনুষ্ঠানিকভাবে ‘একাত্ম’ হিসেবে বিবেচিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু) সম্পর্ক পাতিয়েছিলাম। অন্য সহপাঠীদের মধ্যে দু’একজনের সাথে কদাচিৎ দেখা হয় এখনো, তবে সবার কথা সেভাবে মনেও নেই আর। আসলে ক্লাস থ্রিতে আমি অন্য স্কুলে চলে যাই, আর আমার খাগড়াপুরের সহপাঠীদের অনেকেই পেছনে থেকে যায়, এমনকি মাঝপথে পড়াশুনাই ছেড়ে দেয়।
খাগড়াপুর ছাড়িয়ে
ক্লাস থ্রিতে ওঠার পর আমি আমাদের গ্রাম থেকে এক মাইলের মত দূরের সরকারি প্রাইমারি স্কুলে পড়তে শুরু করি। সেখানে যাঁদেরকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম তাঁদের মধ্যে ছিলেন মদন মোহন চাকমা, মাজেদ স্যার, ডলি তালুকদার, নিরোদবরণ বড়ুয়া। সবচেয়ে যাঁর কথা বেশী মনে পড়ে, তিনি হলেন জ্ঞানতোষ সাহা, ক্লাস ফোর বা ফাইভে ওঠার পর যাঁকে পেয়েছিলাম প্রধান শিক্ষক হিসাবে। মনে পড়ে, তিনি নিজের হাতে আমাকে এবং আমার সহপাঠীদের হাতের লেখা সুন্দর করা শেখাতেন। আমরা যারা বৃত্তি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলাম, তাদের জন্য তিনি বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থাও করেছিলেন। এজন্য তিনি অভিভাবকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ নিয়েছিলেন বলে আমার মনে পড়ে না। বরং বৃত্তি পরীক্ষার সময় তিনি নিজের পকেটের টাকা খরচ করে আমাদের কলা-মুড়ি খাওয়াতেন। তাঁর সস্নেহ পরিচর্যায় আমরা কয়েকজন বৃত্তি পেয়েছিলাম। আমার বন্ধু শান্তি (অকালপ্রয়াত শান্তি প্রিয় চাকমা), যে তখন ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিল, পেয়েছিল প্রথম গ্রেডের বৃত্তি, মাসে ৩০ টাকা হারে। আর আমি পেয়েছিলাম ২৫ টাকা হারে দ্বিতীয় গ্রেডের বৃত্তি। আমার মনে নেই বৃত্তির টাকা হাতে পাওয়ার পর আমরা তাঁকে কোনো উপহার দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম কিনা। কিন্তু এখন বুঝতে পারি যদি সেটা ভাবতামও, তা হত অর্বাচীন চিন্তা। তাঁর কাছে আমাদের যে ঋণ তার কোন প্রতিদান হয় না, টাকার অংকে সে ঋণের কোন মূল্যমানও হয় না।
জ্ঞানতোষ সাহা যে শুধুমাত্র লেখাপড়ায় আমাদের দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন তা নয়, তিনি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও আমাদের প্রেরণা দিয়েছিলেন। তাঁরই উৎসাহে আমি জীবনে প্রথম মঞ্চে উঠি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা আবৃত্তি করতে, ‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির’। বড় হয়ে আমি দু’একবার জ্ঞানতোষ সাহার কথা জানতে চেয়েছি চেনাজনদের কাছে, কিন্তু সেভাবে তাঁর সন্ধান পাইনি। জানি না, তিনি এখনো বেঁচে আছেন কিনা, বা থাকলেও কোথায় কিভাবে আছেন। এটুকু জানি, আমার স্মৃতিতে, এবং আমার মত তাঁর সংস্পর্শধন্য আরো অনেকের স্মৃতিতে, তিনি আজীবন অমর হয়ে আছেন, থাকবেন।
ক্লাস সিক্সে উঠে আমি, শান্তি ও অন্য সহপাঠীরা ভর্তি হই প্রাইমারি স্কুলের লাগোয়া হাই স্কুলে, যেটি তখনও ছিল বেসরকারি স্কুল, তবে পরবর্তীতে ১৯৭৬-এর দিকে পরিণত হয় এখনকার খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। বেসরকারি স্কুল হলেও সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন বেশ কয়েকজন উঁচু মানের শিক্ষক, যাঁরা ছিলেন খাগড়াছড়িতে শিক্ষাবিস্তারের পথিকৃৎ। তাঁদের মধ্যে সবার প্রথমে স্মরণ করছি প্রয়াত নবীন কুমার ত্রিপুরাকে, যিনি ছিলেন আমাদের প্রধান শিক্ষক। উনার পদের কারণে, এবং শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের উপর মাঝে মধ্যে প্রদর্শিত তাঁর সুবিদিত মেজাজের ভয়ে, আমরা উনার কাছ থেকে একটু দূরে দূরেই থাকতাম। কিন্তু মাঝে মধ্যে তিনি শখ করে দু’একটা ক্লাস নিতেন নিচের ক্লাসে, তাখন আমরা বেশ উপভোগই করতাম তাঁর সাবলীল ও সাহিত্যরসমণ্ডিত পড়ানো। তাঁর কাছে ক্লাস সিক্স কি সেভেনে পড়েছিলাম সংস্কৃত, এবং তখন শেখা বিভিন্ন শ্লোকের একটির অংশবিশেষ এখনো আমার কানে বাজে, বিদ্যা এমন ধন, যা ‘চৌরেণাপি ন নীয়তে’ (যে কথার অর্থ হল ‘চোরেরা [চুরি করে] নিতে পারবে না’)। ক্লাস নাইনে উঠে এই ‘হেডমাস্টার স্যার’কে পেয়েছিলাম বাংলার শিক্ষক হিসাবে। আমার বাড়ির কাজের খাতায় লেখা তাঁর মন্তব্য আমাকে উৎসাহিত করত। তাঁর মত শিক্ষকের কল্যাণেই স্কুলজীবনে থাকতেই মুখস্থ বিদ্যা রপ্ত না করেও বাংলায় ক্লাসে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার দক্ষতা অর্জন করেছিলাম আমি, যে ধারা ঢাকায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ার সময়ও অক্ষুন্ন ছিল।
নবীন কুমার ত্রিপুরার মত শিক্ষকের কাছ থেকে যদি সাহিত্য-প্রীতি শিখে থাকি, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে, যুক্তি দিয়ে, বিশ্লেষণ করে কথা বলতে, লিখতে শিখিয়েছিলেন যেসব শিক্ষক, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অনন্ত বিহারী খীসা, যিনি স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। আমার মনে আছে, ক্লাস এইটে তিনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। তিনি যখন ধীর লয়ে ‘দেখি কে বলবে, কে বলবে’ বলতে বলতে ক্লাসের চারিদিকে তাঁর আঙুল ঘোরাতেন, অনেক শিক্ষার্থী যারা পড়া শিখে আসত না, তারা কুঁকড়ে থাকত কোথায় গিয়ে আঙুলটা ঠেকে সে ভয়ে। কিন্তু আমার মনে পড়ে না আমি খুব বেশি ভয়ে থাকতাম, কারণ আমি তাঁর ক্লাসগুলো করতাম মনোযোগ দিয়ে, এবং তাঁর সুপরিমিত ও পরিপাটি, বিনম্র অথচ ঋজু শিক্ষক সত্তার মধ্যে আমি খুঁজে পেতাম অনুকরণীয় অনেক কিছু। খাগড়াছড়িবাসীদের সৌভাগ্য, চাকুরি থেকে অবসর নিলেও অনন্ত বিহারী খীসা এখনো বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে চলছেন বিরল সততা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে। (২০১২ সালের এপ্রিলে আমি সবার শ্রদ্ধাভাজন এই শিক্ষকের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম একটা আত্মজৈবনিক লেখায় হাত দেওয়ার জন্য, বিশেষ করে খাগড়াছড়ির মত জায়গায় শিক্ষাবিস্তারে আজীবন কাজ করে যাওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে। তিনি বলেছিলেন চেষ্টা করবেন। জানি না, ২০২১ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারিতে জীবনাবসানের আগে তিনি কিছু লিখেছিলেন কিনা, তবে আশা করি তাঁর নিজের লেখালেখি বা তাঁকে নিয়ে অন্যদের লেখালেখি সমৃদ্ধ এক বা একাধিক মূল্যবান দলিল আমরা হাতে পাব এক সময়।)
খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের আরো অনেক শিক্ষকের কথাই মনে পড়ে বিভিন্নভাবে যাঁদের কাছে আমি এবং আমার প্রজন্মের আরো অনেকে ঋণী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অশোক কুমার দেওয়ান, নভোজ্যোতি খীসা, অপর্ণাচরণ চাকমা, সতীন্দ্র বিকাশ ত্রিপুরা, হেমন্ত কুমার চাকমা, কৃষ্ণমোহন ত্রিপুরা, পদ্মা তালুকদার ও ধর্মরাজ বড়ুয়া। একজন ‘মৌলবি স্যার’ও ছিলেন, যাঁর আসল নাম মনে পড়ছে না বা কখনো জানা হয়নি, কারণ সবসময় তাঁকে আমরা পূর্বোক্ত নামেই জানতাম। একেক শিক্ষকের সাথে জড়িয়ে আছে একেক ধরনের স্মৃতি। সবার কথা বলে শেষ করা যাবে না স্বল্প পরিসরে। তবু সংক্ষেপে কিছু কথা বলব তাঁদের সাথে জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন স্মৃতির পরিধি বোঝাতে।
প্রথমেই বলি মৌলবি স্যারের কথা। উনার মূল দায়িত্ব ছিল ইসলামিয়াত পড়ানো, তবে তাঁর কাছে আমরা বাংলার মত বিষয়ও পড়েছিলাম। উনি ছিলেন অত্যন্ত নরম প্রকৃতির মানুষ, পিঠে চাপড় মারলেও মনে হত আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। নভোজ্যোতি স্যারের কথা মনে পড়ছে, উনি ক্লাস সিক্সে সম্ভবত সাধারণ বিজ্ঞান পড়াচ্ছিলেন একদিন – ‘চালতা’ কি জিনিস তা আমরা যে ক’জন ত্রিপুরা ছাত্রছাত্রী ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম না। তিনি বিষয়টি ঠিকই মনে রেখেছিলেন, এবং পরের ক্লাসে আমাদের জানালেন চালতা হল ‘তাই প্ল’ (চাকমা ধাঁচে ত্রিপুরা ‘থাই প্ল’ শব্দের উচ্চারণ)। আমরা খুব মজা পেয়েছিলাম, তবে ‘চালতা’ কি, তাও কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম। সতীন স্যার ছিলেন বিজ্ঞানের শিক্ষক, আমাদের পড়াতেন ভূগোল, রসায়ন ইত্যাদি। তবে যতদূর মনে পড়ে তিনি ক্রীড়া শিক্ষকের দায়িত্বও পালন করতেন। তাঁর হাত ধরেই আমি এবং আমার বন্ধু শান্তি প্রথমবারের মত ঢাকায় এসেছিলাম, জুনিয়র রেড ক্রসের জাম্বুরিতে অংশ নিতে। আরেকজন বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন অপর্ণাচরণ স্যার, যিনি একসময় জনসংহতি সমিতির আন্দোলনে অংশ নিতে চলে যান (এবং ১৯৮৩ সালে অন্তর্ঘাতে নিহত হন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সহ আরো কয়েকজন সহযোদ্ধাসমেত)। অশোক কুমার দেওয়ানকে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলাম স্বল্প সময়ের জন্য, ক্লাস নাইনে। আমরা জানতাম তিনি কলকাতার গ্র্যাজুয়েট, ছিলেন সুদর্শন, এবং তাঁর বেশভূষা (ধুতি পরতেন), বাচনভঙ্গী, জ্ঞান, মেধা সব কিছু মিলিয়ে তিনি সম্ভবত ছিলেন খাগড়াছড়ির মত জায়গায় কলকাতা-কেন্দ্রিক বিদ্বৎসমাজের একজন অপ্রত্যাশিত কিন্তু অনন্য প্রতিভূ। বয়স ছোট বলে তাঁর প্রজ্ঞা, গবেষক মনন ও ইতিহাসমনস্কতা স্কুলে পড়ার সময় ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারিনি, সেটা বুঝেছি আরো বড় হয়ে, তাঁর কিছু লেখা পড়ে। যে শিক্ষকদের কথা বললাম, তাঁরা প্রায় সবাই এখন পরলোকে। (এই লেখা প্রথম যখন লিখেছিলাম, কৃষ্ণমোহন স্যার ও হেমন্ত স্যার জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা উভয়েই প্রয়াত হন ২০১৪ সালে।)
আমাদের মাঝে এখনো আছেন ধর্মরাজ বড়ুয়া, যাঁর সাথে কদাচিৎ দেখা হয় খাগড়াছড়ি গেলে। আর একজন শিক্ষক পদ্মা তালুকদারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করব, যদিও তাঁর সাথে ব্যক্তিগতভাবে অনেকদিন কোনো যোগাযোগ নেই আমার। ক্লাস এইটে তিনি সম্ভবত বাংলা দ্বিতীয় পত্র পড়াতেন আমাদের। একবার কি একটা দরখাস্ত লিখতে দিয়েছিলেন অনুশীলনী হিসেবে। মনে আছে, আবেদনের শেষে বিনয়ের আতিশয্যে এবং নূতন লেখা শব্দ জাহির করতে গিয়ে আমি লিখেছিলাম, প্রার্থনা মঞ্জুর হলে আমি ‘মহোদয়ের চির কিংকর হইয়া থাকিব’ (কিংকর অর্থ ভৃত্য)। পদ্মা তালুকদার আমাকে বলেছিলেন, কৃতজ্ঞতার যত কারণই থাকুক, কারো কাছে ‘চির কিংকর’ হয়ে থাকার কারণ নেই। তাঁর সে উপদেশ আমি মনে রেখেছি।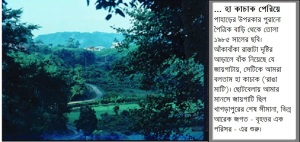
পৃথিবীর পথে
১৯৭৬/৭৭ সালের দিকে খাগড়াছড়ি হাইস্কুলের সরকারিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়াতে আমাদের অনেক শিক্ষক প্রশিক্ষণে চলে গেলে ক্লাস টেনে ওঠার পর আমাকে বাবা-মা পাঠিয়ে দেন রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। আমার সহপাঠী পুলক জীবন খীসাও চলে এসেছিল রাঙ্গামাটিতে। সেখানে আমি থাকতাম আয়ং (জেঠা) বরেন ত্রিপুরার বাসায়, আইনচুক (জেঠি/বড় মাসি) নন্দা ত্রিপুরার মাতৃস্নেহের ছায়ায় (তিনি ছিলেন আমার মায়ের বড় বোন)। আয়ং বরেনের সান্নিধ্যেই আমি বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম ককবরক সাহিত্য ও ত্রিপুরাদের ইতিহাসের প্রতি। আমি রাঙ্গামাটি যাওয়ার আগে থেকেই আয়ং যখন কোনো কাজে খাগড়াছড়িতে এসে আমাদের বাড়িতে উঠতেন, আমি তাঁর ব্যাগ ঘাঁটতাম বিভিন্ন আগ্রহ-উদ্দীপক পাণ্ডুলিপি পড়ার লোভে। কাজটা গর্হিত ছিল হয়তবা, তবে এ কাজে আমি আয়ং-এর প্রশ্রয় পেয়েছিলাম। রাঙ্গামাটিতে থাকা অবস্থায় আয়ং-আইনচুকের ছোট ছেলে নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরার সান্নিধ্য পেতাম যখন তিনি ছুটিতে বাড়ি আসতেন। সেসময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। আমি ও আমার ভাইয়েরা তাঁকে ডাকতাম ‘দা চিকন’ নামে। মনে পড়ে, একবার রাঙ্গামাটিতে আমার লেখা একটা কবিতা পড়ে তিনি কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা আমার জন্য অশেষ প্রেরণার উৎস হয়েছিল। (পরে আমিও ঢাকায় পড়তে যাওয়ার পর দা চিকনকে আরো কাছে পেয়েছিলাম, এবং আমি একটা স্কলারশিপ পেয়ে আমেরিকায় পড়তে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বিবিধ ক্ষেত্রে তাঁর প্রভূত সহায়তা, পরামর্শ ও উৎসাহ পেয়েছিলাম।)
রাঙ্গামাটিতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফল প্রত্যাশী আরো অনেকের মত আমিও পড়েছিলাম ‘পণ্ডিত স্যার’ নামে পরিচিত বিপুলেশ্বর দেওয়ানের কাছে। তিনি ছিলেন একজন জীবন্ত কীংবদন্তী। সেসময় তিনি কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না, কিন্তু তিনি একাই হয়ে উঠেছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান, একটি মহীরুহ, যার ছায়ায় লালিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। পণ্ডিত স্যারের পড়ানোর ধরন, প্রথাগত মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে শিক্ষণীয় বিষয়ের মৌলিক দিকগুলোকে ভালভাবে রপ্ত করানোর পদ্ধতি, আমাকে – এবং আমার মত আরো অনেককেই – সারা জীবনের অমূল্য সঞ্চয় দিয়েছে।
রাঙ্গামাটি গভর্মেন্ট হাই স্কুলে পুলক আর আমি বেশিদিন পড়িনি। তবে সেখানে অনেক দক্ষ শিক্ষকের সস্নেহ পরিচর্যা পেয়েছিলাম আমরা। আর পরবর্তী জীবনের অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুও আমরা খুঁজে পাই রাঙ্গামাটিতে গিয়ে, যদিও অনেকেই এখন প্রবাসী বিধায় তাদের সাথে আর নিয়মিত যোগাযোগ নেই। মফস্বল থেকে আসা হিসেবে আমি আর পুলক অবশ্য প্রথম দিকে কিছুটা আড়ষ্ট থাকতাম, তবে আমাদের ‘ভালো ছাত্র’ পরিচয় জেনে অনেকেই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এক্ষেত্রে স্কুলের তখনকার প্রধান শিক্ষক এমদাদুল ইসলামেরও একটা ভূমিকা ছিল। তিনি আমাকে এবং আমার বন্ধু পুলককে কাছে টেনে নিয়েছিলেন আপন সন্তানের মত করে (তাঁর এক ছেলেও ছিল আমাদের সহপাঠী), এবং এসএসসিতে আমাদের ফলাফল ভালো হওয়ার পর তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেছিলেন, ‘তোমাদের দু’জনকে আরো আগে থেকে পেলে আমি তোমাদেরকে বোর্ডে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড স্ট্যান্ড করিয়ে ছাড়তাম’। (স্ট্যান্ড করা বলতে বোঝাত বোর্ডের মেধা তালিকায় প্রথম বিশ জনের মধ্যে স্থান পাওয়া।) আমাদের ‘ভালো’ ফলাফল ছিল আপেক্ষিক অর্থে, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায়। আমি কুমিল্লা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় পঞ্চদশ স্থান পেয়েছিলাম, এবং আর মাত্র চার নম্বর বেশি পেলে পুলকও চলে আসত প্রথম বিশ জনের মধ্যে। খাগড়াছড়িতে আমাদের পুরানো শিক্ষকদের অনেকের নাকি আক্ষেপ ছিল, তাঁদের গড়া দু’জন ছাত্রের ভালো রেজাল্টের কৃতিত্ব নিয়েছিলেন অন্যরা। শুনেছি, আমাকে রাঙ্গামাটি যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যাপারেও আপত্তি ছিল দু’একজন শিক্ষকের। সেটির পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল। শিক্ষক সংকট থাকলেও যাঁরা তখনো ছিলেন, তাঁরা ছিলেন খুবই নিবেদিতপ্রাণ, তাঁরা অবশ্যই সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন আমাদের ভাল ফল পেতে সাহায্য করতে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল খাগড়াছড়িতে থেকে যাওয়া আমাদের বন্ধু শান্তি (অকালপ্রয়াত শান্তিপ্রিয় চাকমা)। সে খাগড়াছড়ি থেকে পরীক্ষা দিয়েই বাণিজ্য বিভাগে এসএসসির মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছিল।
‘স্ট্যান্ড’ করার সুবাদে জীবনে বহু প্রশংসা শুনেছি, পেয়েছি বহু মানুষের আশীর্বাদ। তবে এ বিষয়টিকে ঘিরে খুব হৃদয়স্পর্শী একটা কাহিনীও রয়েছে, যেটির কেন্দ্রে আছেন ‘দাদা মাস্তর’ বা রামকৃষ্ণ ত্রিপুরা। আমি যে বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলাম, সে বছর একটি খুনের ঘটনায় মিথ্যে অভিযোগ বা সন্দেহের ভিত্তিতে তাঁকে আটক করে দীঘিনালায় নিয়ে গিয়েছিল সরকারি এক সংস্থা। সেখানে, বন্দী অবস্থায়, একদিন মেঝেতে পড়ে থাকা একটি পত্রিকার টুকরায় নাকি তাঁর নজরে পড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের খবর, যেখানে মেধা তালিকায় ছিল আমার নাম! বন্দীদশার ক্ষোভ, কষ্ট আর গ্লানির মাঝে বিষয়টি তাঁর কাছে ছিল এক ঝলক আনন্দের দমকা হাওয়ার মত। ঘটনাটি তিনি আমাকে নূতন করে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন এ লেখায় হাত দেওয়ার কয়েক মাস আগে, খাগড়াপুরে পৃথ্বীরাজের দোকানে চা খাওয়ার ফাঁকে। তখন আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, মুক্তি পাওয়ার পর তিনি আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন, সেখানেও সম্ভবত উল্লেখ করেছিলেন ঘটনাটা।
যে সময়ের কথা বলছি, তখন খাগড়াছড়িতে সড়ক-যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই অনুন্নত, এবং টেলিফোন বা বিদ্যুতের বালাই ছিল না। খাগড়াছড়ি থেকে রাঙ্গামাটিতে যেতেই আমাদের লেগে যেত প্রায় পুরো একদিন। রওনা হতে হত খুব ভোরে। ঋতু ভেদে ‘চাঁদের গাড়ি’, নৌকা, পদযুগল ও লঞ্চের বিবিধ সমন্বয়ে বেলা শেষে পৌঁছাতাম রাঙ্গামাটিতে। রিজার্ভ বাজারের কাছে যখন পৌঁছাতাম, কখনো সন্ধ্যা হয়ে আসলে লঞ্চ থেকে বৈদ্যুতিক আলোতে এলাকাটি মোহনীয় লাগত। এরপর ঘাটে নেমে শুনতাম বেবি ট্যাক্সির শব্দ, যা খাগড়াছড়িতে ছিল না। তখন মনে হত, আরেক পৃথিবীতে চলে এসেছি। চিটাগাং বা ঢাকাও আমরা তখন যেতাম রাঙ্গামাটি হয়েই। দূর থেকে বাড়ির সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য চিঠিই ছিল প্রধান ভরসা।
জীবনে একসময় চিঠি যে আমি কত লিখেছি, কত পেয়েছি, তার কোনো হিসেব নেই। নিয়মিত লিখতাম মা-বাবা, ভাইদের, এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের। আমি আমেরিকায় যাওয়ার পর এই তালিকা আরো লম্বা হয়েছে, এবং বেড়েছে আমার চিঠি লেখার মাত্রাও। ইমেইল, ফেসবুক ও মোবাইল ফোনের কল্যাণে এখন হাতে লেখা চিঠির চল প্রায় সম্পূর্ণ উঠে গেছে। আমি নিজে ১৯৯০-এর দশকের পর বিশেষ কাউকে হাতে লেখা চিঠি পাঠিয়েছি, বা তেমন কারো চিঠি পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। অন্যদের বেলায়ও নিশ্চয় তাই। তবে আমার প্রজন্মের মানুষদের কাছে পুরানো আমলের চিঠিপত্রের একটা বিশেষ আবেগিক মূল্য রয়েছে, এবং আমার দৃষ্টিতে এগুলির ঐতিহাসিক মূল্যও রয়েছে। বাড়িতে একটা ট্রাংকে সযত্নে রক্ষিত ছিল আমার এ ধরনের চিঠিপত্রসহ পুরানো দিনের ছবি, ছেলেবেলায় লেখা কবিতা, ডায়েরি ইত্যাদি। কিন্তু একদিন চরম বিস্ময় আর বেদনার সাথে আবিস্কার করি, সেই ট্রাংকের ভেতরে সবার অগোচরে উই পোকা বাসা বেঁধেছে। আমার কাছে মহামূল্য, এমন অনেক কিছুই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সবেচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিলাম যখন আমি দেখতে পাই আমার মায়ের লেখা চিঠির বান্ডিলটা ছিল উইয়ের আক্রমণের প্রধান শিকার। যাহোক, সেই ট্রাংকের পুনরুদ্ধারকৃত কাজগপত্র থেকে বাছাই করা বাবা ও মায়ের একটি করে চিঠির নির্বাচিত অংশবিশেষ নিচে তুলে ধরছি আমার ফেলে আসা দিনগুলির কিছু খণ্ডচিত্র হিসেবে।[২]
বাবার চিঠি
রামগড়
২৯/১২/১৯৮১পিনতু
তোমার সর্বশেষ ২৭/১২/৮১ এর [এবং আগের একাধিক] চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। কিন্তু নানান কাজের ঝামেলায় এ পর্যন্ত কোন উত্তর দেওয়া হয়নি। আজ […] ৫০০/- টাকার একটা ড্রাফট পাঠাচ্ছি। হাতে টাকা না থাকার কারণে ৬০০/- টাকা পাঠানো সম্ভব হলো না। এ মাসের বেতন পেলে আরও ১০০/- টাকা পাঠাবো। তোমাদের পরীক্ষার বা ভার্সিটির খবরাদি জানাবে।
গত ২৪/১২/৮১ ইং তারিখে রাঙ্গামাটি গিয়েছিলাম [ত্রিপুরা] সংসদের কাজে। আমাদের সংসদের প্রকাশিত ম্যাগাজিনে ছাপানো [একটা] আর্টিকেল নিয়ে রাঙ্গামাটিতে তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি হয়েছে। তারা সবাই একজোট হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে […।…] আমি ২৫/১১/৮১ ইং তারিখের বিকেলে সুরেনবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। সুরেনবাবু বিলেত থেকে ফিরেছেন। তাঁর ও পরিবারের সকলের সংগে দেখা হয়েছে। রাঙ্গামাটি কলেজের কয়েকজন ছাত্র ও অন্যান্য কয়েকজন প্রতিবেশীর সংগেও দেখা হয়েছে। তাঁদের সংগে প্রায় [দেড়-দুই]ঘন্টা ধরে আলাপ করেছি। দীর্ঘ আলাপের পর তাদের সংসদের প্রতি বিরূপ মনোভাব অন্ততঃ ৫০% নিরসন করতে পেরেছি বলে মনে হলো। এ নিয়ে আমি পরবর্তী কালে রাঙ্গামাটিতে একটি বিশেষ অধিবেশন আহবান করার আশা রাখি।
[…] শুনলাম […] সংসদকে বা ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে রাঙ্গামাটির লোকদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখিত চিঠিপত্র ইত্যাদির প্রতিবাদ করে নাকি তুমি একটা লেখা পাঠাবে। এ বিষয়ে [কেউ] তোমাকে কিছু লিখতে বলেছেন কিনা জানি না। তাই বলি, যদি সেরকম হয়ে থাকে, তাহলে কারো প্রভাবে বা কারো অনুরোধে যেন তুমি কিছু [না লেখো]। নিজের থেকে লিখলে যেন স্বাধীন সত্তা নিয়ে [লেখো]। […]
তুমি [ককবরক] ভাষায় সংকলন বের করার জন্য সংসদ থেকে যে টাকার কথা লিখেছ, তা বোধ হয় দেওয়া সম্ভব হবে না। কারণ রাঙ্গামাটির ‘সাকনি কক্ প্রচার সংসদ’কে ইতিপূর্বে দেওয়া হয়নি। এ অবস্থায় তোমাকে বা সালকাতাল [ক্লাব]-কে কোন মঞ্জুরী দিলে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে।
এ বৎসর ধান খুবই কম হয়েছে। মাত্র ৩০০/৪০০ আড়ি পাওয়া গেছে। মোটেই বিক্রী করা যাবে না। তোমাদের পড়ার খরচ যে কেমন করে চালাব ভেবে পাচ্ছি না। কাজেই তোমাকে একটু মিতব্যয়ী হতে বলি।
জানতে পারলাম যে, Indian scholarship এর জন্য advertise [করা] হয়েছে। তুমি apply করেছ কিনা? এ ব্যাপারে তুমি একবার বলেছিলে এক বৎসর loss দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু আমাদের দেশে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে এখন যে অবস্থা, তাতে তোমাদের course শেষ হতে চার বৎসরের জায়গায় ৬/৭ বৎসর লাগবে না তাই বা কে বলতে পারে। তাই আমি বলি তুমি সুযোগ থাকলে যে কোন scholarship avail করো।
[…]
আমি আগামী ২/১/৮২ বাড়ী যাবো খাগড়াছড়িতে সংসদের অফিস অডিট করা হবে ৪, ৫, ৬ তারিখে। কাজেই উক্ত অডিট চলাকালীন আমাকে সেখানে থাকতে হবে।
হিলট্র্যাক্ট্স-এর অবস্থা এখন মোটামুটি শান্ত। ভারত থেকে সব শরণার্থী ফিরে এসেছে এবং যার যার জায়গায় চলে গেছে। […]
বাড়ীর অন্যান্য খবর ভালো। আশীর্বাদ জেনো।
‘বাবা’
মায়ের চিঠি
খাগড়াপুর
১১/৫/৮২পুতুং
গতমাসের চিঠিতে তোমার আমেরিকায় যাওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত খবর জেনে খুবই আনন্দ পেলাম। আমিও গতমাসের শেষ দিকে একখানা পাঠিয়েছিলাম, তা হয়তো এতদিনে পেয়েছ। আজকের বিশেষ খবর হল, এখানে দীর্ঘদিন একটানা খরা হচ্ছে। ভীষণ দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখতেছি। বলতে গেলে আমরাওতো চাষা। তাই আমাদেরও আর্থিক উন্নতির আশা দেখতেছি না। আমাদের জায়গা জমি শুকিয়ে মাটী ফেটে উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। অন্যান্য বছরে এ মৌসুমে জমি চাষ হয়ে থাকে কিন্তু এখন কিছুতে সম্ভব হচ্ছে না।
তোমাদের কলেজ হোস্টেলের খাওয়া, দাওয়া কেমন চলতেছে, তা অবশ্য আমি জানি না। তবু চিন্তা করতে হয়, কিভাবে খাচ্ছ। যাক দশ জনের জন্য যা অবস্থা তোমার বেলায়ও তা হতে হবে। তবু মাতৃত্বের আর্তনাদ, কোন মা[ই] সন্তানদের জন্য চিন্তা না করে থাকতে পারে না। এখন আমার আরো বেশী করে নানা দিক থেকে মনে [ভার] বেড়ে আসবে। কেননা তোমরা সবাই দূর দূরান্তে বিদেশ বিভুঁয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিচ্ছ। রিনতুওতো তেমনি। মোটামুটি রিনতু ক্যাডেটে ভর্ত্তি হতে পারলে বাড়ীতে সানতু আর আমি, সেও আর কতদিন, তারও বাইরে যাওয়ার খুব ইচ্ছা। এসব কথা লিখতেছি বলে মন খারাপ করবেনা, নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে না। [এমনটা] সব মায়েদেরই খেয়াল এবং স্বভাব।
এই গ্রীষ্মের দিনগুলো কেমন যেন নীরবতা অনুভব করি। বিরাট একটা বাড়ী, চারিদিকে বাগান। প্রকৃতির ছন্দে ছন্দে, বৈশাখের মুখরতা আর আম কাঁঠালের সমারোহ। এই বৈশাখ প্রতিটি বছর ঘুরে আসবে, বৃদ্ধি পাবে গাছে গাছে ফুল ফল, অথচ আমাদের বাড়ীর পরিবেশ কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আঙিনা ভরা পাড়া প্রতিবেশীদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দেখে তোমাদের শৈশবের কথা মনে ভেসে উঠে। আবার কখনোবা নিজের মনকে এই বলে বুঝিয়ে [সান্ত্বনা] পেয়ে থাকি যে, হ্যাঁ, আমার ছেলেরা সবাই সুযোগ্য সন্তান, তাই তারা আর কেন ঘরকুনো হয়ে বসে থাকবে? কেউবা আবিস্কারের দিকে পা বাড়াচ্ছে, কেউবা যাচ্ছে দিগ্বিজয়ী হতে। তোমাদের গৌরবে, আমাদের মুখোজ্জ্বল হবে। এই আশা রেখে আজকের লেখা শেষ করছি।
[পুনশ্চ:] আর একটা কথা লিখছি। কক্বরক সম্মেলনে তোমার একটা কিছু লেখা পাঠালে না কেন? অন্যান্য যারা ছোট ছোট প্রবন্ধ তৈয়ার করেছে মোটামুটি ভাল হয়েছে। বাচ্চুর একটা এসেছে। সুরেন বাবু, রণজিৎবাবু তাঁরাও দিয়েছেন। নয়ং [বরেন ত্রিপুরা] তো থাকবেই। সবচেয়ে ভাল লেগেছিল যশোবর্ধন ও ব্রজনাথের [লেখা]; বড় গবেষকদের প্রবন্ধগুলো বুঝতে কিন্তু কঠিন [লাগে]। বাচ্চুর লেখাটা পাঠ করেছে রীতা, সুরেন বাবুর স্বপন, রণজিতের সুরজিত, আরগুলো উপস্থিত থেকে নিজের লেখা পাঠ করেছে। সংসদের বার্ষিক অধিবেশনও একসাথে হয়েছে। বাড়ীর চিঠিপত্র ঠিকমতো পেয়ে থাক কিনা জানাবে। তোমার স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখবে। মাঝে মাঝে বাইরে খাওয়ার ব্যবস্থা করবে। আমরা মোটামুটি শারীরিক কুশলে রয়েছি। রিনতুও আপাতত বাড়ীতে। আশীর্বাদ করে শেষ করছি।
ইতি
মা
সাল কাতাল
খাগড়াপুরে সাল কাতাল নামে একটা ক্লাব আছে। নামের অর্থ (নূতন সূর্য/দিন) থেকেই বোঝা যায়, যারা এর প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ছিল, তাদের প্রণোদনা কি ছিল। এ ক্লাবের উদ্যোক্তারা ছিল আমার প্রজন্মের কিছু তরুণ, যারা কৈশোর পেরুনোর আগেই এটির প্রতিষ্ঠায় হাত দিয়েছিল। আমার ট্রাংকে রক্ষিত কাগজপত্র ঘেঁটে আমি উদ্ধার করেছি, শুরুতে মূলত একটা পাঠাগার তথা যুব-কিশোর সংগঠন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমার সভাপতিত্বে জুলাই ৭, ১৯৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১২ জন ছাত্রের একটি সভা। সেখানে সংগঠনের নাম ঠিক করা হয়েছিল শুধু একটি শব্দে, ‘সংঘ’, যার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয় যথাক্রমে ললিত চন্দ্র ত্রিপুরা ও প্রবীর ত্রিপুরাকে। কালক্রমে এই সংঘই রূপ নেয় সাল কাতাল ক্লাবে, যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছিল ১৯৮১ সালের দিকে, তৎকালীন ত্রিপুরা সংসদের সভাপতি বি. কে. রোয়াজার হাতে। আমি নিজে যেহেতু ততদিনে খাগড়াছড়ির বাইরেই থাকতাম পড়াশুনার কাজে, সাল কাতাল ক্লাবের নিয়মিত সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে আমার তেমন সম্পৃক্ততা ছিল না। কিন্তু যখনই সুযোগ পেতাম, ছুটে যেতাম খাগড়াপুরে, সেখানে মেতে উঠতাম ক্লাবের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে।

১৯৮১ সালের দিকে বর্তমান লেখকের সম্পাদনায় সালকাতাল ক্লাব প্রকাশিত দেওয়াল পত্রিকা ‘বুখ্রৈ’ (ককবরক শব্দটি ‘কুঁড়ি’ বোঝায়)
বলা বাহুল্য, সাল কাতাল ক্লাবের পেছনে আমাদের বাবা-মা সহ অন্যান্য অভিভাবকরাও উৎসাহ জুগিয়েছিলেন, বিশেষ করে মা। যতদূর মনে পড়ে, ক্লাবের নামটাও চূড়ান্ত করা হয়েছিল মার উৎসাহেই। সাধারণভাবে বাবা-মা দু’জনেই তাঁদের সন্তানদের মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা, শৈল্পিক মনোবৃত্তি এবং সমাজমনস্কতা সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের প্রজন্মের আলোকে যে মূল্যবোধ বা নীতি-আদর্শকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করেছিলেন, সেগুলি নিজেদের জীবনে পুরোপুরি ধারণ করতে সদাসচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের অনুসৃত মূল্যবোধ ও নীতি আদর্শকে যদি এক কথায় প্রকাশ করতে হয়, তা হয়ত হবে ‘মানবতাবাদ’। খাগড়াছড়িতে আমাদের বাড়িতে বৈঠকখানায় দাদা-দাদির পেন্সিলে আঁকা স্কেচ আর নানা-নানির ফটোগ্রাফের পাশাপাশি টাঙানো থাকত রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ছবি। আর ছিল মার হাতে করা সূচিশিল্পের দু’টি নমুনা – একটিতে তাজমহল, আরেকটিতে গৌতম (বুদ্ধ)-কে নৈবেদ্য দিতে আসা সুজাতার চিত্রায়ন। বাবা-মা ছিলেন সনাতন ধর্মের অনুসারী, কিন্তু আমাদের বাড়ির বৈঠকখানায় কোনো পৌরাণিক দেব দেবীর ছবি দেখিনি কখনো। কোনো রাজা-রাজড়া বা রাজনৈতিক নেতার ছবিও কখনো টাঙানো হয়নি সেখানে। তবে বৈঠকখানার এক কোনায় ছিল একটি বইয়ের আলমারি। সেখানে পাশাপাশি রাখা থাকত গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল। ছিল বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থও, এবং একটি বাংলা কোরআন। আবার সেগুলির পাশেই ছিল সঞ্চয়িতা, গীতবিতান এবং নজরুলের ‘সঞ্চিতা’র মত গ্রন্থ। ছিল তারাশঙ্করের বেশ কিছু উপন্যাস। অন্য যেসব লেখকের বইপত্র ছিল তাদের মধ্যে যেসব নাম মনে পড়ে সেগুলির মধ্যে রয়েছে শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, জরাসন্ধ, শংকর, যাযাবর, বনফুল, রুডিয়ার্ড কিপলিং, ম্যাক্সিম গোর্কি, সিগমুন্ড ফ্রয়েড। কার্ল মার্ক্সের বইও ছিল। ছিল বিশ্বকোষ। সময়টা ছিল খাগড়াছড়িতে বিদ্যুৎ বা টেলিভিশন আসার অনেক আগেকার। আমার মধ্যে বই পড়ার নেশা প্রবল হয়ে ওঠার পর একটার পর একটা বই শেষ করতে থাকি। হারিকেন ল্যাম্পের আলোতে পড়তাম বেশ রাত করে।
আমি আমার পড়া বইপত্রসহ অনেক বিষয় নিয়েই মার সাথে কথা বলতাম নিয়মিত। মাকে নিয়ে আমি মজাও করতাম সুযোগ পেলেই। মনে পড়ে, আমেরিকায় পড়তে যাওয়ার সময় তাঁকে বলেছিলাম, সাথে একজন বিদেশিনীকে নিয়ে ঘরে ফিরব। মা বলেছিলেন, ‘সমস্যা নেই, কিন্তু পড়াশুনাটা আগে ঠিকমত শেষ করো, তারপর তোমার নিজের যাকে পছন্দ জীবনসঙ্গিনী বানাও’। অবশ্য আমার বিয়ে কেন, পড়াশুনার শেষটাও মা দেখে যেতে পারেননি। তাঁকে শেষবার দেখেছিলাম ১৯৮৪-এর গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বাড়িতে এসে, আমি আমেরিকা যাওয়ার এক বছরের মাথায় ধরা পড়া ক্যান্সারে পর্যুদস্ত অবস্থায় মৃত্যুপথযাত্রী এক রোগী হিসেবে। ছুটি শেষে আবার ফিরে গেলাম আমেরিকায়। তখনই জানতাম, জীবদ্দশায় এই নশ্বর পৃথিবীতে আমি আর মাকে কোনোদিন দেখব না। আমি চলে যাওয়ার মাস দুয়েকের মাথায় মার মৃত্যুর খবর পাই, বাবার পাঠানো একটা চিঠিতে, যা পেয়েছিলাম মার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দুই সপ্তা পরে। চিঠিটা বেশ ভারী ছিল, যা হাতে পেয়েই বুঝে গিয়েছিলাম ভেতরে কি খবর আছে। আমি খামটা খুলিনি সারাদিন, বুঝিবা তাতে এই পৃথিবীতে মা আরো কিছুক্ষণ বেঁচে থাকতেন, অন্তত আমার কাছে। মার তুলনায় বাবার মৃত্যু ছিল অনেক বেশি পরিণত বয়সে। তবে পৃথিবীতে কেইবা আপনজনদের মৃত্যুকে সহজে মেনে নিতে পারে! যাহোক, আমার সৌভাগ্য যে, বাবার বেলায় তিনি রোগশয্যায় থাকা অবস্থায় তাঁর কিছুটা কাছে থাকতে পেরেছিলাম আমি। তখন তাঁর কাছ থেকে বেশ কিছু বিষয় জেনেছিলাম যেগুলি আগে জানতাম না। জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে তিনি আমাকে নিয়ে তাঁর একটা ইচ্ছার কথাও বলেছিলেন। সেটা ছিল এই যে, আমি যেন পিএইচডিটা শেষ করি। ত্রিপুরাদের মধ্যে প্রথম পিএইচডিধারীর তকমাটা তাঁর সন্তানের গায়ে উঠবে, এটা হয়তবা তাঁর ইচ্ছার মূলে ছিল। আসলে শুধু আমার প্রয়াত বাবাই না, আমার অন্য আরো একাধিক স্বজনেরও এমন আশা ছিল, যেমন তাদের মধ্যে আমাকে নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্নও ছিল, এখনো হয়ত আছে: কেন আমি ট্র্যাক পাল্টে নৃবিজ্ঞান পড়তে গিয়েছিলাম, কেনই বা আমেরিকা থেকে চলে এসেছিলাম, ইত্যাদি। এগুলির উত্তর দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন বা অবকাশ বর্তমান লেখায় নেই, তবে প্রাসঙ্গিক দু’একটি কথা এখানে বলা যায়।
আসলে আমেরিকায় কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে যাওয়ার দু’বছরের মধ্যেই আমার মধ্যে একটা সংকট তৈরি হয় -আমি আসলেই একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী হতে চাই কিনা তা নিয়ে। গণিত ও বিজ্ঞানে আমি বেশ ভালই ছিলাম বরাবর, এবং কম্পিউটার নিয়ে পড়াশুনা শুরু করার পর প্রথম দিকে সেটি বেশ উপভোগও করছিলাম। কিন্তু মাঝপথে এসে যন্ত্রের বদলে মানুষ নিয়ে পড়াশুনার আগ্রহ কিভাবে যেন আমার মধ্যে জেঁকে বসে। একদিন ঘুম থেকে উঠে ঠিক করলাম, আমি কম্পিউটার বিজ্ঞান বাদ দিয়ে নৃবিজ্ঞান পড়ব। নূতন বিষয়ে পড়া আমার জন্য ছিল এক ধরনের শেকড়ের সন্ধান, নিজেকে জানার, নিজের অতীতকে বোঝার একটি প্রয়াস। জানি না, মাকে হারানোর ধাক্কা আমার অবচেতন মনে এই তাড়না নিয়ে এসেছিল কি না। যাহোক, নৃবিজ্ঞান, এবং সাথে কিছুটা ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে আমি পড়াশুনা চালিয়ে যাই নূতন উৎসাহে। উল্লেখ্য, পড়াশুনার ব্যাপারে আমার আগের সব সিদ্ধান্তই ছিল অনেকটা সময় ও পরিবেশের, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিমণ্ডলের সামাজিক চাহিদার, চাপিয়ে দেওয়া। “তোমার মাথা ভাল, সুতরাং বিজ্ঞান পড়। ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্ট ভাল হয়েছে? এখন ঠিক করো কি হবে: ডাক্তার না ইঞ্জিনিয়ার? বুয়েটে চান্স পেয়েছ, কি পড়বে ঠিক করেছ? ইলেকট্রিক্যালের ডিমান্ডটাই বেশি, সুতরাং সেখানেই যাও। আমেরিকায় একটা স্কলারশিপ – সেতো সোনার হরিণ! সেটির দেখা যখন পেলেই, পড় কম্পিউটার সায়েন্স!” তখনো বিল গেটস বা স্টিভ জবসদের নাম শোনেনি বিশ্ব। তবে আমি আমেরিকায় পড়ার দু’তিন বছরের মধ্যেই ক্যাম্পাসে চলে আসে অ্যাপল ডেস্কটপ। তার আগে আমরা ব্যবহার করতাম মেইনফ্রেম কম্পিউটার, আলাদা টার্মিনালে যার যখন ইচ্ছা বা প্রয়োজন লগ ইন করে। একবার দেখেছিলাম, সবচেয়ে বেশি লগ-ইন করাদের তালিকায় আমার নাম ছিল শীর্ষে। সেই আমি কিনা হঠাৎ করে সেই ইঁদুর দৌড় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলাম একেবারে!
যাহোক, নৃবিজ্ঞানে যথাসময়ে স্নাতক পর্যায় শেষ করার পর আমি পিএইচডি পর্বের অধ্যয়নের জন্য বেছে নিয়েছিলাম ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে আমি মোট চার বছর ছিলাম। বার্কলেতে সব মিলিয়ে আমার ভালোই সময় কাটছিল, কিন্তু একটা পর্যায়ে পিএইচডির কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটে পড়ে যাই আমি, এবং একসময় সব ছেড়েছুড়ে দেশে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। এই লেখার পরিসরে আমার তখনকার ব্যক্তিগত সংকট নিয়ে তেমন কিছু বলার নেই, তবে প্রসঙ্গত নিজের একটা অভিমতের কথা উল্লেখ করতে পারি। আমেরিকা ছেড়ে চলে আসার সময় আমার সত্যি মনে হয়েছিল, এখনো মনে হয়, আপাতত ত্রিপুরাদের মধ্যে কোনো পিএইচডি ডিগ্রিধারী না হলেও চলবে। বরং আমাদের মধ্যে যেটা বেশি করে দরকার সেটা হচ্ছে সাক্ষরতা, মৌলিক শিক্ষা ও নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। শিক্ষার আলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে না পড়লে ত্রিপুরাদের মত সতত বঞ্চিত-নিগৃহীত-নিপীড়িত জাতির মুক্তি আসবে না। এটি শুধু ত্রিপুরাদের বেলায় কেন, অন্যান্য বহু প্রান্তিক জাতির বেলায়ও প্রযোজ্য। শিক্ষা মানে এখানে আমি শুধু সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি নির্ভর পড়াশুনার কথা বলছি না, বলছি এমন জ্ঞান অর্জনের কথা যা গণমানুষের কল্যাণ আনবে, বলছি এমন আদর্শ ও নীতি ধারণ করার কথা যা আমাদেরকে শুধু ত্রিপুরা, পাহাড়ি বা বাংলাদেশি করে রাখবে না, বরং উৎসাহিত করবে মানুষের মত মানুষ হতে, বিশ্বনাগরিক হতে। সেই কাঙক্ষিত ‘সাল কাতাল’-এ পৌঁছাতে হলে এখনো অনেক ত্যাগ, অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হবে আমাদের।
নূতন দিনের আলোর দিশারীদের উদ্দেশ্যে দু’টি কথা
এই লেখা শুরু করেছিলাম বাবা-মাসহ ফেলে আসা দিনগুলির আলোর দিশারীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের তাগিদ থেকে। কিন্তু শেষ করতে চাই নূতন দিনের আলোর দিশারীদের প্রতি দু’টি কথা বলে। এই লেখা, বা যে আয়োজনকে ঘিরে এটি লিখেছি, তা মাথায় ঘুরপাক খাওয়ার পর থেকে আমার মনে হয়েছে, যেখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু, সেই খাগড়াপুরে এখন শিক্ষার পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কেমন, তা নিয়ে একটু খোঁজ নেওয়া দরকার। খাগড়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, যেখানে আমার শিক্ষাজীবন শুরু, এখন কতজন লেখাপড়া করে? কেমন করছে তারা? সালকাতাল ক্লাবের সাথে কারা এখন সংশ্লিষ্ট? কি তারা করে? জানলাম, প্রবীর, আমার ভাই, উভয় প্রতিষ্ঠানের সাথে এখনো যুক্ত। তার মাধ্যমে যেটুকু তথ্য পেয়েছি, তাতে হতাশ হওয়ার মত কোনো কারণ দেখিনি, বরং আশান্বিত হয়েছি এটা জেনে যে, পাড়ার স্কুলে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় একশ’ ভাগ শিক্ষার্থীই পাশ করেছে পর পর দুই কি তিন বছর (২০১২ সালের জানুয়ারির তথ্য)। খুশি হয়েছি পাড়ার দু’একজন সন্তান খাগড়াপুরের বাইরের স্কুলে ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে বা বৃত্তি পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে শুনে। তবে শুধু হাতে গোনা কয়েকজনের বিরল কৃতিত্বে তুষ্ট থাকলে হবে না, আমাদের নজর দিতে হবে সকল শিক্ষার্থীর গড়পড়তা মানের উপর। আর এক্ষেত্রে শুধু জিপিএ’র মানদণ্ডে শিক্ষার মান যাচাই করলে চলবে না, খেয়াল রাখতে হবে শিক্ষার্থীরা আসলে কি শিখছে, ক্লাসের বাইরে তারা কি করছে, কি ধরনের স্বপ্ন দেখছে, ইত্যাদি বিষয়ের উপর। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকদের, সমাজের প্রত্যেকের, অনেক দায়িত্ব আছে। খাগড়াপুর স্কুল সরকারি হয়েছে বলে আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়েছে, তা ভেবে বসে থাকলে চলবে না। তার উপর “আমার সন্তান যেহেতু অন্যখানে পড়ছে, পাড়ার স্কুল নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর আর কিছু নেই,” এমন ভাবাটা হবে আমাদের পূর্বসূরীদের শেখানো পথ থেকে সরে আসা। আমাদের বাবা মায়ের ঋণ, জ্ঞানতোষ সাহার মত আমাদের ছোটবেলার শিক্ষকদের ঋণ শোধ করতে হবে রক্তের সম্পর্ক থাক বা না থাক, আশেপাশের সকল শিশুকে নিজের সন্তান মনে করে শিক্ষাদানে সহায়তা করার মাধ্যমে।

লেখকের ভাগ্নি সম্পর্কের জয়ন্তী ত্রিপুরা ‘নতি’ (১৯৮৪~৮৫ সালের ছবি), যে এখন তার বাবা – আমাদের ‘দাদা মাস্তর’ – রামকৃষ্ণ ত্রিপুরার মতই একজন শিক্ষক। (ছবির স্বত্ত্ব – লেখক)।
আমি প্রবীরের কাছে একটা তথ্য পেয়ে বেশ চমৎকৃত হয়েছি – খাগড়াপুর এখন শিক্ষকে ভরা। একসময় খাগড়াপুরেই শিক্ষাজীবন শুরু করেছে, এমন অনেকে এখন বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষকতার সাথে জড়িত, প্রায় সবাই প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে। এমন শিক্ষকের সংখ্যা হবে পঞ্চাশ জনের মত, যা অবশ্যই উল্লেখ করার মত সংখ্যা। এছাড়া খাগড়াপুরে এখন প্রায় আধ ডজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছেন, যাঁরা চাকুরি থেকে অবসর নিলেও সমাজে ব্যাপক অর্থে তাঁদের শিক্ষক সত্তা ধরে রাখছেন, রাখবেন, এটি আমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা।
আমরা এমন এক সময়ে এমন এক দেশে বাস করছি যেখানে ব্যাপকভাবে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে, শিক্ষাঙ্গনে চলছে পেশীশক্তির দৌরাত্ম্য। আমি দশ বছর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছি। তখনই দেখেছিলাম শিক্ষাঙ্গনের অবস্থা কেমন সংকটাপন্ন। এ লেখা যখন লিখছি (জানুয়ারি ২০১২), তখন জাবিতে তথা সারা দেশে তোলপাড় চলছে একজন শিক্ষার্থীর হত্যাকাণ্ড নিয়ে। সমাজে প্রকৃত শিক্ষকদের মর্যাদা অনেকটাই কমে গেছে আগের তুলনায়। তেমন শিক্ষকদের কাছে না গিয়ে শিক্ষার্থীরা, এমনকি শিক্ষকরা, অনেকে ছুটছেন ক্ষমতার সাথে যুক্ত মানুষদের পেছনে। দেশের সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষাঙ্গনে যখন এ অবস্থা চলছে, দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থা কি, তা সহজে অনুমেয়। সেখানে হয়ত সন্ত্রাস বলতে যা বোঝায় তা নেই, কিন্তু আছে অব্যবস্থাপনা, অবহেলা। আর আছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি একটা সামষ্টিক অবজ্ঞা, প্রচলিত সামাজিক মানদণ্ডে। এই অবস্থায় স্রোতের বিপরীতে পথ চলা খুব কঠিন। কিন্তু ঠিক এ কারণেই তা আবার খুব জরুরিও। তা না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আলোকিত পথের নিশানা খুঁজে পাবে না, তারা তলিয়ে যাবে হিংসার ঘূর্ণাবর্তে, আটকে থাকবে মানসিক দীনতা ও ক্ষুদ্রতার অন্ধকারে, ভেসে যাবে ভোগ্যপণ্যের তোড়ে।

পারিবারিকভাবে আয়োজিত জানুয়ারি ১৯, ২০১২ তারিখের একটি শিক্ষক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রামকৃষ্ণ ত্রিপুরা উপহার তুলে দিচ্ছেন নবীন প্রজন্মের শিক্ষক ঊষারাণী ত্রিপুরার হাতে। ছবিতে বসা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে (বাম থেকে) জাতীয় পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের স্বীকৃতি পাওয়া চন্দ্র কিশোর ত্রিপুরা ও খাগড়াপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশা প্রিয় ত্রিপুরা।
নূতন আলোর পথের দিশারীরা, আপনারা কত বেতন পান, তা দিয়ে নিজেদের মূল্য নিরূপণ করবেন না। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা, বা তাদের স্তাবক ও অনুচরবৃন্দ আপনাদের সম্মান না দিলেও বিচলিত হবেন না। মনে রাখবেন, আপনার দিকে তাকিয়ে আছে অনেক শিশু। আপনার প্রতিটি কথা, প্রতিটি পদক্ষেপ তাদের কচি মনে স্থায়ী ছাপ রেখে চলছে। আপনি একটু যত্নবান হলে, একটু স্নেহ ও মমতা দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ালে, কে জানে, আপনার হাতেই গড় উঠতে পারে এমন কেউ যে হিংসায় বিক্ষুব্ধ এই পার্বত্য চট্টগ্রামে, বা এমনকি এই পৃথিবীর জন্য, একজন যোগ্য নেতা হিসেবে গড়ে উঠবে। সে হবে এমন এক নেতা, যার কাছে আপনি হবেন চিরনমস্য। সে হতে পারে এমন এক রাষ্ট্রনায়ক, যার কাছে সুশিক্ষা ও শিক্ষকদের আসন থাকবে সবার উর্ধে। তবে আপনাদের শিক্ষার্থীরা কেউ যদি বড় মাপের কোনো নেতা হয়ে নাও ওঠে, ক্ষতি নেই। তাছাড়া নেতা মানেই শুধু রাজনৈতিক নেতা, তাতো নয়। আপনার হাতে গড়া দশটি শিশু যদি স্রেফ মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে, তাও অনেক। আপনারা পঞ্চাশ জনে মিলে এমন পাঁচশ জন মানুষ উপহার দিতে পারেন খাগড়াছড়িকে, তাতে অনাগত প্রজন্মের জন্য আগামী দিনের খাগড়াছড়ি, আগামী দিনের পৃথিবী নিশ্চয় আরো একটু বাসযোগ্য, আরো একটু সুন্দর হয়ে উঠবে। নূতন দিনের আলোর পথের দিশারীরা, এই মহৎ কর্তব্য সাধনে আপনাদের জানাই অন্তরের অন্তস্থল থেকে অভিবাদন ও শুভকামনা।
টীকা
[১] এই লেখাটি প্রথম উপস্থাপন করা হয়েছিল লেখকের প্রয়াত মা-বাবা, সরলিকা ওরফে সুরধ্বনি ত্রিপুরা (জন্ম আনুমানিক ১৯৪২ – মৃত্যু অক্টোবর ৬, ১৯৮৪) ও ব্রজেন্দ্রনাথ ত্রিপুরা (জন্ম আনু. ১৯৩৭ – মৃত্যু সেপ্টেম্বর ২৮, ২০০৮)-র স্মরণে খাগড়াছড়ির খাগড়াপুরে জানুয়ারি ১৯, ২০১২-তে পারিবারিকভাবে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে, যেখানে খাগড়াপুরনিবাসী মোট নয়জন শিক্ষককে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক – বেলা রোয়াজা, ব্রজনাথ রোয়াজা, রামকৃষ্ণ ত্রিপুরা, ভুবন মোহন ত্রিপুরা, প্রার্থনা কুমার ত্রিপুরা ও ধনমোহন ত্রিপুরা – এবং তিনজন কর্মরত কৃতী শিক্ষক, যথাক্রমে, ২০১১ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া চন্দ্রকিশোর ত্রিপুরা, আগে বিভাগীয় পর্যায়ে একই ধরনের স্বীকৃতি পাওয়া সত্য প্রকাশ ত্রিপুরা ও খাগড়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশা প্রিয় ত্রিপুরা। এছাড়া খাগড়াপুরনিবাসী ও জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কর্মরত প্রায় ৫০ জন শিক্ষক ও এলাকার কৃতী শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপহার দিয়ে সম্বর্ধিত করা হয়, এবং শিশু-কিশোরদের জন্য আয়োজিত রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। এই লেখার প্রাথমিক খসড়ার উপর মূল্যবান মতামত দিয়ে এটিকে পরিশীলিত করতে সহায়তা করেছিলেন অজয় ত্রিপুরা, কল্লোল রোয়াজা ও প্রবীর ত্রিপুরা। বর্তমান ভাষ্যটি ২০১২ সালে উপস্থাপিত মূল লেখার ঈষৎ সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত রূপ [যা, বন্ধনীর আগ পর্যন্ত বর্তমান টীকাসমেত প্রকাশিত হয়েছে উৎসব নামে খাগড়াছড়ি থেকে প্রকাশিত ও প্রদীপ চৌধুরী সম্পাদিত একটি সংকলনে (২য় সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৫)। তবে এই ব্লগে প্রকাশের জন্য লেখাটিতে সামান্য কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে, এবং বেশ কিছু ছবি যোগ করা হয়েছে যেগুলির প্রায় সবই (একটি বাদে) জানুয়ারি ২০১২’র অনুষ্ঠানে বিলি করা ভাষ্যে ছিল। এছাড়া লেখাটির অংশবিশেষ ফেসবুক নোট আকারেও প্রকাশিত হয়েছে আগে।]
[২] চিঠি দুইটির উদ্ধৃতাংশসমূহে সম্পাদিত ও বাদ দেওয়া জায়গাগুলি আয়ত বন্ধনীতে দেখানো হয়েছে। অন্যথায় ভাষা ও বানানরীতি মূলানুগ রাখা হয়েছে। ‘পিনতু’ ও ‘পুতুং’ হল বাড়িতে/গ্রামে ব্যবহৃত আমার দুইটি ডাকনাম।


শ্রদ্ধেয় স্যারে লেখা পড়ে আমারও ১০-১৫ বছরের ফেলে আসা দিনগুলো মনে পরে গেলো।